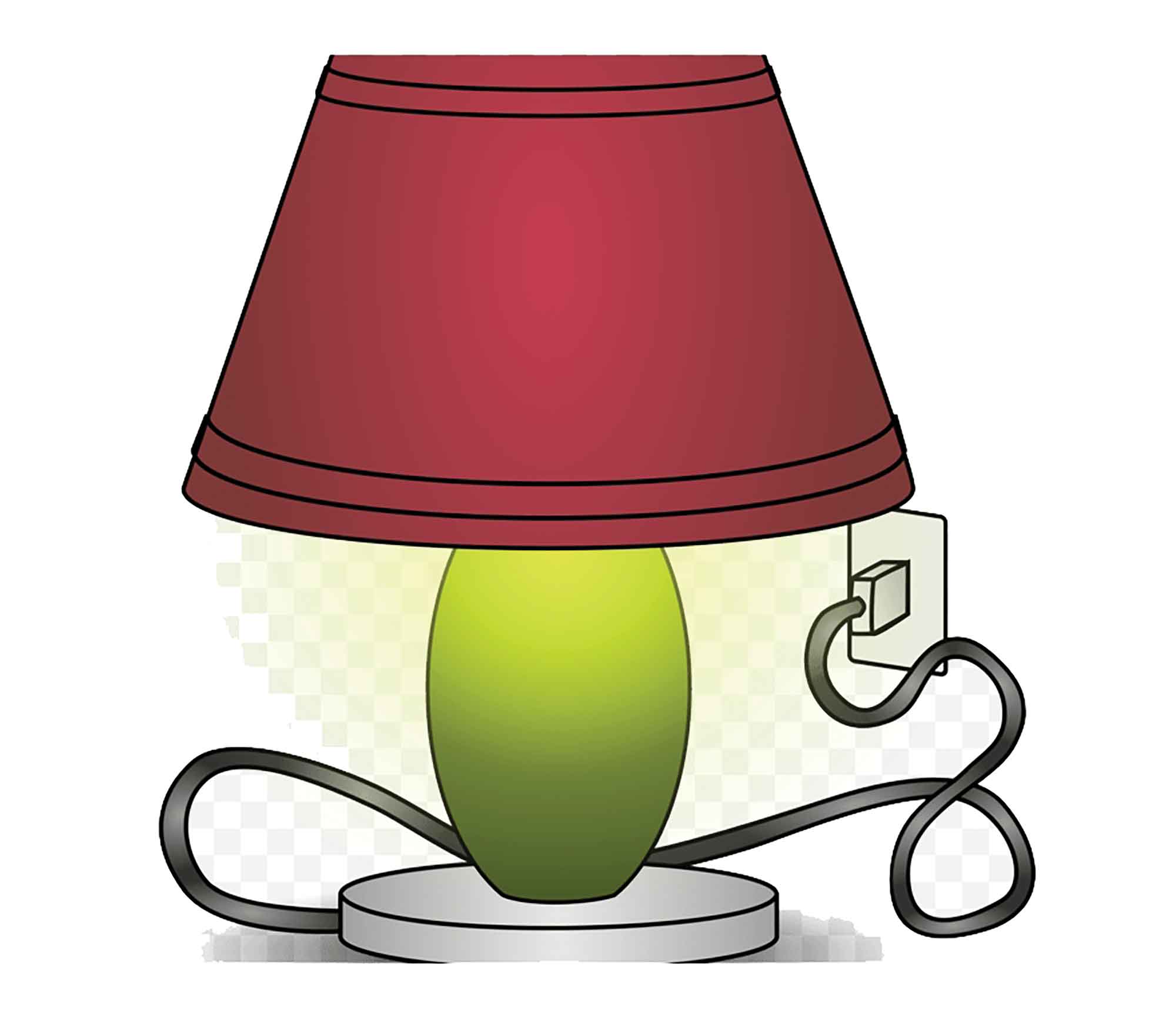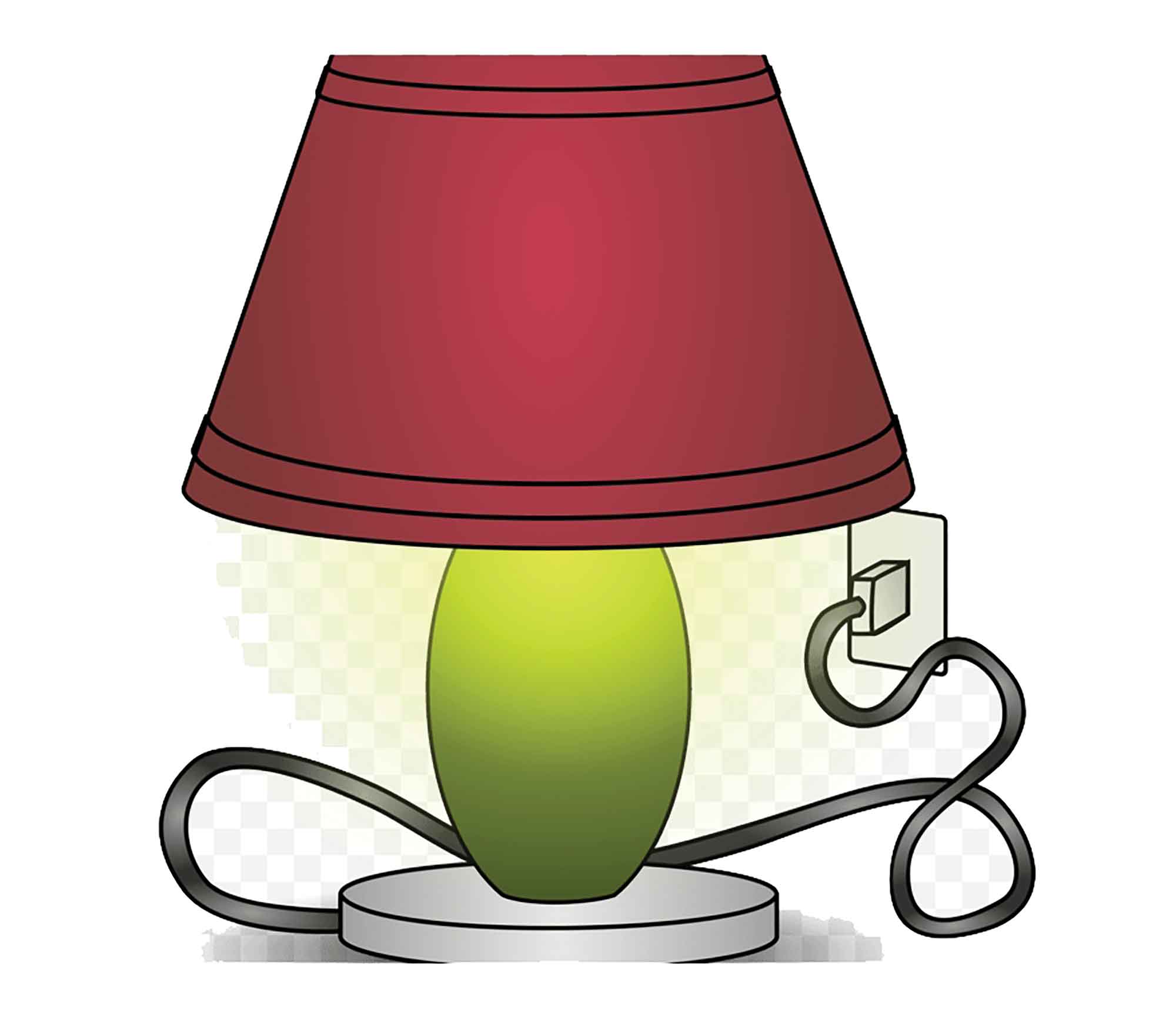বাতি
বাতির ব্যবহার অতি প্রাচীন। সাধারণত বাতি বলতে বুঝায় কুপি, টর্চ লাইট, হ্যারিকেন,লণ্ঠন, হ্যাজাক। বাতি হলো সেই সরঞ্জাম যা অন্ধকার দূর করতে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকালে আগুনের ব্যবহারের মাধ্যমে বাতির প্রচলন হয়। অতীতে লাইট হাউসের বাতির মাধ্যমে সমুদ্রের জাহাজের দিকনির্দেশনা দেওয়া হতো।
বাতির শ্রেণিবিভাগ : তেল বাতি : প্রাচীনকালে খনিজ তেল এবং প্রাণিজ তেল ব্যবহার করে বাতি জ্বালানো হতো। খনিজ তেলের মধ্যে কেরোসিন তেল অন্যতম। কেরোসিন কুপি, হ্যারিকেন, মশাল, হ্যাজাক। এসব বাতির প্রধান জ্বালানি ছিল কেরোসিন। তবে কিছু ক্ষেত্রে প্রাণিজ উদ্ভিদ তেল ব্যবহৃত হতো।
বৈদু্যতিক বাতি : বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে বর্তমানে অনেক প্রকার বাতির আবিষ্কার হয়েছে। বর্তমানে বৈদু্যতিক বাতির ব্যাপক ব্যবহার হয়। আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে বাতির কর্ম ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। টিউব লাইট, বিদু্যৎ সাশ্রয়ই বাতি, হ্যালোজেন লাইট ও ফ্লুওরসেন্ট লাইট।
রাসায়নিক বাতি : স্প্রিট ল্যাম্প ও মোম বাতি।
বাতির ব্যবহার : অন্ধকার দূরকরণে বাতির ব্যবহার সার্বজনীন। স্থান কাল ভিন্নতার কারণে বাতির ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।
১. গৃহে সাধারণত কম আলো প্রদানকারী বাতি ব্যবহার হয়। প্রাচীনকালে গৃহে কুপি এবং হ্যারিকেন বাতি ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে বিদু্যৎ সাশ্রয় বাতি ব্যবহার হয়।
২. শিল্প-কারখানায় অতি উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন হয়, তাই এখানে বৈদু্যতিক বাতি প্রধান উৎস। শিল্প-কারখানায় উচ্চ শক্তির বাতি ব্যবহার হয়।
৩. সংগীত ও সিনেমায় বাতির ব্যবহার হয়। সিনেমা জগতে লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন বলে চিত্র ধারণ করা হয়।
৪. কম্পিউটারে মনিটরে এলইডি, এলসিডি বাতি ব্যবহার করা হয়। ল্যাম্প সফটওয়্যার- যাতে অ্যাপাচি, মাইএসকিউএল সমর্থন করে।
বৈদু্যতিক বাতি আবিষ্কারের ঘটনা:১৮০২ সালে বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি সর্বপ্রথম বৈদু্যতিক বাতি তৈরি করেন। তার তৈরিকৃত বাতির নাম ছিল আর্ক ল্যাম্প। এই বাতি বেশিক্ষণ টিকতে পারত না। মূলত একটি নির্দিষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালালে সেই পদার্থ আলোকশক্তি উৎপন্ন করে। বাতির উন্নতি সাধনে সবচেয়ে বেশি যিনি ভূমিকা রাখেন, তিনি হলেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তার তৈরিকৃত বাতি বাসাবাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী ছিল। তাকেই আধুনিক বৈদু্যতিক বাতির জনক বলা হয়।
ইনক্যানডেসেন্ট বাল্ব: বর্তমানে 'বাল্ব' শব্দটি উচ্চারণ করলে যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাকেই ইনক্যানডেসেন্ট বাল্ব বলে। বাতির ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে ইনক্যানডেসেন্ট বাল্ব জ্বলে ওঠে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ভরা এক কাচের খোলসে এই ফিলামেন্ট রাখা হয়। ফিলামেন্ট হিসেবে টাংস্টেন নামের এক দুর্লভ ধাতু ব্যবহার করা হয়। এই পদার্থ আলোকে আরো উজ্জ্বল করত। এছাড়াও এই বাতির উৎপাদন ও শক্তির খরচ ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক কম।
হ্যালোজেন বাল্ব : হ্যালোজেন বাল্বের কাচের ভেতরে আবদ্ধ গ্যাস থাকে। হ্যালোজেন বাতিতে ব্যবহার করা হয় হ্যালোজেন গ্যাস। হ্যালোজেন গ্যাস হিসেবে এই বাতিতে শুধু ব্রোমিন ও আয়োডিন ব্যবহার করা হয়। ১৮৮২ সালে প্রথম হ্যালোজেন বাল্ব তৈরি হলেও তা ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। ১৯৫৫ সালে দুজন প্রকৌশলী এলমার ফ্রিডরিখ ও এমেট ওয়াইলি সর্বপ্রথম ব্যবহারযোগ্য হ্যালোজেন বাতি তৈরি করেন। হ্যালোজেন বাতির মূল সুবিধা হলো, এতেও ফিলামেন্ট হিসেবে টাংস্টেন ব্যবহার করা হয়। তবে অন্যান্য বাতির তুলনায় এটি খুব বেশি উজ্জ্বল। তাই কর্মক্ষেত্রে এই বাতির ব্যবহার বেশি করা হয়। অনুষ্ঠানে মঞ্চের আলো, চলচ্চিত্র নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হ্যালোজেন বাতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে এই বাতির কিছু অসুবিধাও রয়েছে। অসুবিধাগুলোর মধ্যে উলেস্নখযোগ্য হলো- এই বাতিগুলো ভীষণ গরম হয়। তাই জ্বালানো অবস্থায় খালি হাতে এগুলো ধরার সাহস করা উচিত নয়। তাছাড়া হ্যালোজেন বাল্ব বিস্ফোরিত হতে পারে।
ফ্লুওরেসেন্ট বাল্ব : পদার্থবিজ্ঞানে বস্তুর 'আলোক প্রতিপ্রভা' বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে আসে ফ্লুওরেসেন্ট বাল্ব। এদের কম্প্যাক্ট ফ্লুওরেসেন্ট লাইট বা সিএফএল বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন, কিছু নির্দিষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন চালনা করলে তা আলোক প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। তখন থেকেই ফ্লুওরেসেন্ট বাতি নিয়ে কাজ শুরু হয়। ১৯৭৬ সালে অ্যাডওয়ার্ড হ্যামার নামের এক বিজ্ঞানী প্রথম সিএফএল তৈরি করেন। তিনি একটি ফ্লুওরেসেন্ট টিউবকে পেঁচিয়ে তা দিয়ে এই বাতি তৈরি করতে সক্ষম হন। এই টিউবের মধ্যে আর্গন গ্যাস ও সামান্য পরিমাণ বাষ্পায়িত পারদ থাকে। টিউবের ভেতরের অংশে ফসফোর নামক এক আলোক প্রতিপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ লেপন করা হয়। এই টিউবের মধ্য দিয়ে বিদু্যৎ চালনা করলে তীব্র ঔজ্জ্বল্য সহকারে সাদা আলো জ্বলে ওঠে। সিএফএল আসার মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলো তৈরি করা সহজতর হয়। এই বাতিতে ব্যবহৃত টিউবের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজটি করা হয়। আলো সাদা হলেও ভিন্ন বর্ণের টিউব হওয়ায় আলোর বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটে। আমরা বর্তমানে বাসায় যে টিউব লাইট ও পেঁচানো টিউবের বাল্ব ব্যবহার করি, তা এই সিএফএল বাতি।
এলইডি বাল্ব : এলইডির পুরো নাম হলো লাইট এমিটিং ডায়োড। এলইডি বাতি বলতে মূলত অনেক ছোট ছোট বাতিকে বোঝায়। এরকম অনেকগুলো ছোট বাতি একত্রিত করে বেশি আলো সংবলিত বাল্বের আকার দেওয়া যায়। তাছাড়া ঘর আলোকিত করা ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বাসার সৌন্দর্যবর্ধনে এখন এলইডি ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বাতি তেমন গরম হয় না, নির্দিষ্ট সময় পর অকেজো হয়ে পড়ে না। তাই বর্তমানে এদের ব্যবহার তুলনামূলক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ বাতির ব্যবহার শিখেছে। বিদু্যৎ শক্তিকে যখন মানুষ পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে আনতে পারে, তখন থেকেই মানব জাতির জন্য নতুন এক যুগের সূচনা হয়। বিদু্যৎ সহজলভ্য হওয়ার পর থেকে আবিষ্কৃত হতে থাকে নানা বিদু্যৎ চালিত যন্ত্র। এসব যন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে অন্যান্য সব ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সভ্যতার বিকাশের পথে তাই এই বিদু্যৎচালিত যন্ত্রগুলোর ভূমিকা কখনো অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন বিদু্যৎ চালিত যন্ত্রের মাঝে একটি হলো বৈদু্যতিক বাতি বা লাইট বাল্ব। বিদু্যৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত করার পর থেকে যাত্রা শুরু হয় লাইট বাল্বের।
হ শিক্ষা জগৎ ডেস্ক