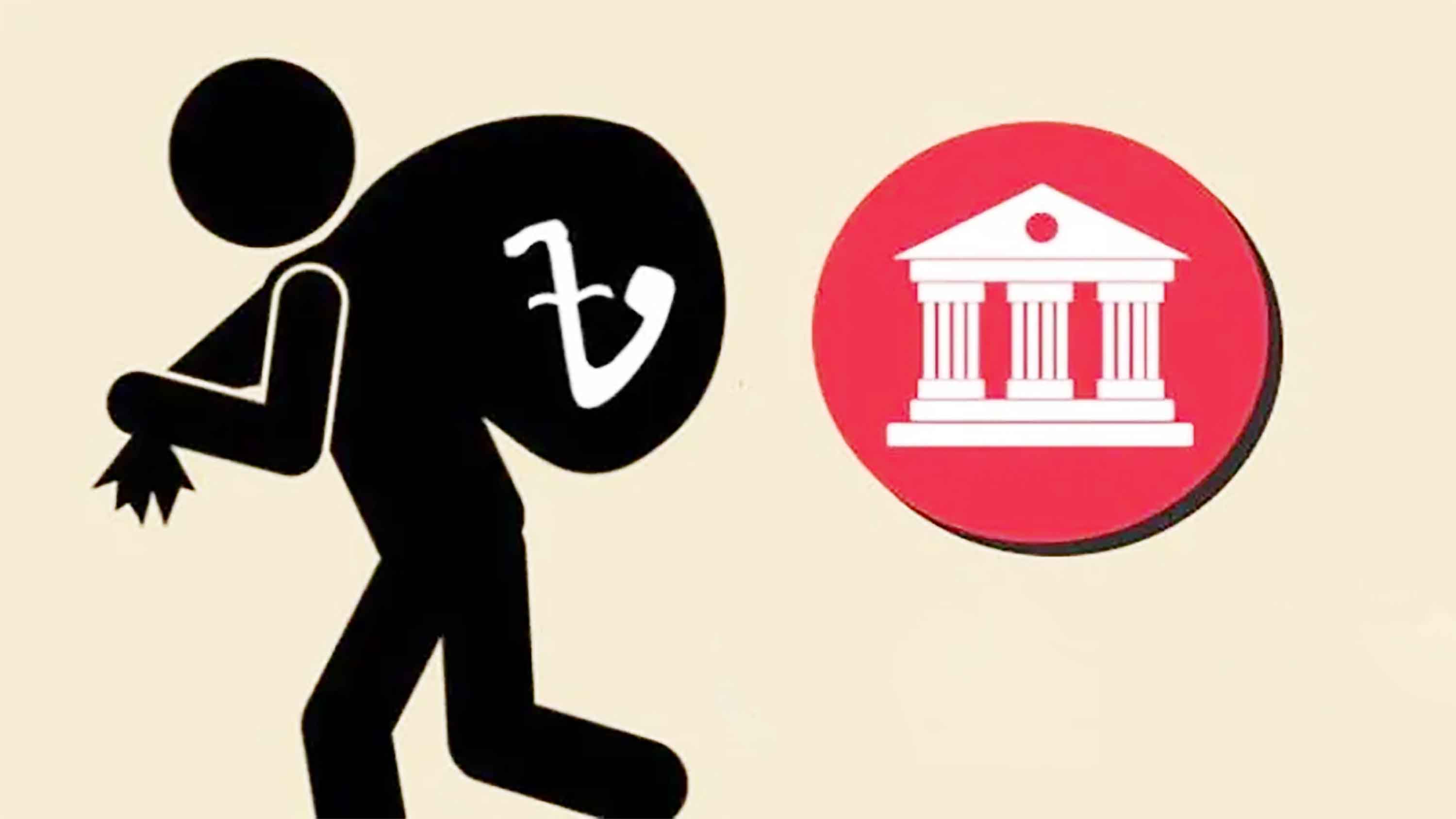
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ- যা গত কয়েক দশক ধরে উলেস্নখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অগ্রগতির পথে কিছু বড় বাধা রয়েছে- যার মধ্যে ঋণখেলাপি এবং দুর্নীতি উলেস্নখযোগ্য। এই দুটি সমস্যা শুধু দেশের ব্যাংকিং খাতকেই দুর্বল করছে না, বরং দেশের সাধারণ মানুষকেও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যদিও সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে, তবুও এই দুটি সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
একটি দেশের অর্থনীতির দর্পণ হলো সেই দেশের শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ব্যাংকিং খাতের উন্নতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায়ক। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এখনো কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি- যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো বছরের পর বছর লোকসান গুনছে এবং কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা দিতে পারছে না। অন্যদিকে, বেসরকারি ব্যাংকগুলো উন্নত দেশের ব্যাংকিং কাঠামো অনুসরণ করতে চাইলেও, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু অনভিজ্ঞ এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত নীতিনির্ধারকদের জন্য তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে, ক্ষমতাবান রাজনৈতিক এবং অপরাধীরা দুর্নীতি ও অর্থ-পাচারের মতো কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই পরিচালনা করছে।
বাংলাদেশে ঋণখেলাপির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এত দিন বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করেছে। গত সরকারের আমলে বাছবিচার না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় বেসরকারি ব্যাংকের উলেস্নখযোগ্য সংখ্যক লাইসেন্স দিয়েছে। ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে ঋণখেলাপির তালিকায় নাম ওঠে। সাধারণত ঋণ নেওয়ার পর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ব্যাংকের কাছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দেশের আর্থিক খাত মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকা। একটি দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণের পরিমাণ। তবে এটি প্রকৃত চিত্র নয়। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ, ঋণ অবলোপন এবং মামলাধীন ঋণ যোগ করলে এই পরিমাণ ছয় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে- যা আর্থিক ব্যবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে। বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকার আমলে রাজনৈতিকভাবে লাইসেন্স পাওয়া তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের কিছু ব্যাংক মৃতপ্রায় হয়ে আছে। জনগণের করের টাকায় এসব ব্যাংক বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে লুটপাট রাজনৈতিক প্রভাবেই তা অনস্বীকার্য। অর্থনীতির তোয়াক্কা না করে এই ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং নয় বরং জনগণের অর্থ লোপাটেই যেন বেশি মনোযোগী, দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী এরা। বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারের বেশিরভাগ ব্যাংকিং সংস্কার পদক্ষেপ খেলাপিদের পক্ষে গেছে।
ঋণ খেলাপির প্রবণতা বাড়ার পেছনে বেশ কিছু বিশেষ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো- ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক যাচাই-বাছাইয়ের অভাব, ঋণগ্রহীতাদের অর্থের অপব্যবহার এবং সরকারের তরফ থেকে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপের অভাব। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী বা রাজনীতিবিদরা ব্যাংক থেকে বিশাল অঙ্কের ঋণ নিয়ে তা ফেরত দেন না এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। একক ব্যক্তি বা গ্রম্নপ কোনো একটি ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ অর্থ ঋণ নিতে পারবে, তা ঋণ সীমা নীতিমালায় বলা আছে। কিন্তু একক ব্যক্তি বা গ্রম্নপ একাধিক ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ ঋণ নিতে পারবে, সেটা আইনে না থাকায় মোটা অংকের ঋণ নিয়ে খেলাপি হওয়ার সুবিধা প্রভাবশালী ব্যবসায়ীগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে।
ঋণখেলাপির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত আরেকটি সমস্যা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২ থেকে ৩ শতাংশ জিডিপি দুর্নীতির কারণে হারিয়ে যায়। এই দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে না, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরে বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।
দুর্নীতি ব্যাংকিং খাতেও বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তারা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে বা ঘুষের বিনিময়ে তাদের ঋণ প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকের পরিচালকরা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তারা প্রভাবশালী ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধায় ঋণের বাণিজ্যিক অবস্থান যাচাই না করেই বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণের মাধ্যমে বের করে নিয়েছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কাগজপত্র ছাড়াই বিশাল অঙ্কের ঋণ মঞ্জুরি করা হয়- যা পরবর্তী সময়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়।
ঋণখেলাপি এবং দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপি হয়, তখন ব্যাংক সেই ক্ষতি পূরণের জন্য সুদের হার বাড়িয়ে দেয়, যা সাধারণ ঋণগ্রহীতাদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি, ব্যাংকগুলোতে সঞ্চয় রাখা মানুষেরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। কারণ, ব্যাংকগুলোর মুনাফা কমে গেলে তারা কম সুদ দেয় এবং মানুষের সঞ্চিত অর্থ থেকে মুনাফা কমে যায়।
এছাড়া, ছোট এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা (এসএমই) যারা মূলত ঋণ নিয়ে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে, তারাও এই দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, ঋণ নেওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দরকার, তারা অনেক সময় ঋণ পায় না, বরং প্রভাবশালীরা সহজেই বিশাল ঋণ পেয়ে যায়। ফলে, প্রকৃত উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে না, যার প্রভাব দেশের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনের ওপর পড়ে।
বর্তমান সরকার ঋণখেলাপি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ আদায়ের জন্য কঠোর নীতি প্রণয়ন করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করার সুবিধাও প্রদান করেছে। তবে এই পদক্ষেপগুলো এখনো যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। কারণ, ঋণখেলাপির সংখ্যা বাড়ছেই এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী ঋণখেলাপিরা কোনোরকম শাস্তি ছাড়াই পালিয়ে যাচ্ছে।
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম শক্তিশালী করা, বিভিন্ন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা করা। কিন্তু দুর্নীতির মূল কারণগুলোকে দূর করতে হলে আরও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
ঋণখেলাপি এবং দুর্নীতির সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমেই দরকার কঠোর আইনি কাঠামো এবং এর যথাযথ প্রয়োগ। ব্যাংকিং খাতের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় কঠোর নিয়মাবলি পালন করতে হবে। ঋণ গ্রহীতাদের প্রাথমিক যাচাই-বাছাই এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হবে। পাশাপাশি, ঋণগ্রহীতাদের দায়িত্বশীলতার ওপর জোর দিতে হবে এবং ঋণখেলাপি হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে দেশের জনগণের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। এছাড়া, দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও ক্ষমতাশালী করতে হবে এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
যারা বৃহৎ ঋণখেলাপি তাদের গৃহীত ঋণের বিপরীতে কি পরিমাণ সম্পদ আছে তা বিস্তারিতভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। এই সম্পদগুলো বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যেতে পারে, তা দিয়ে ঋণের পরিমাণ পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব কিনা, তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পুরোপুরি আদায় করা না যায়, তাহলে সংশ্লিষ্টদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হলে বিদ্যমান আইন সংশোধন করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
সুশাসন এবং জবাবদিহিতার অভাবে ঋণখেলাপি এবং দুর্নীতি বেড়ে যায়। সুতরাং, সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। একমাত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারি এবং দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে পারি।
ঋণখেলাপি এবং দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা সমাধান করতে হলে সরকার, ব্যাংকিং খাত এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, বরং সেই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতার মাধ্যমেই আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি।
মাহমুদুল হাসান : এফসিসিএ, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, পিকেএসএফ